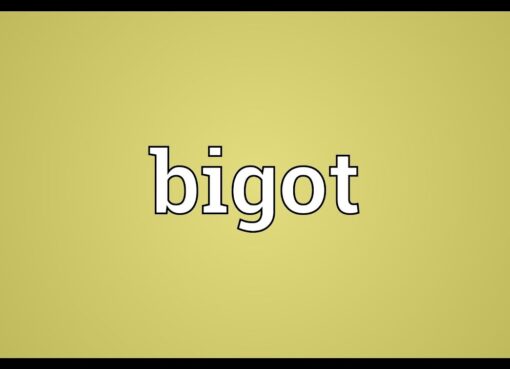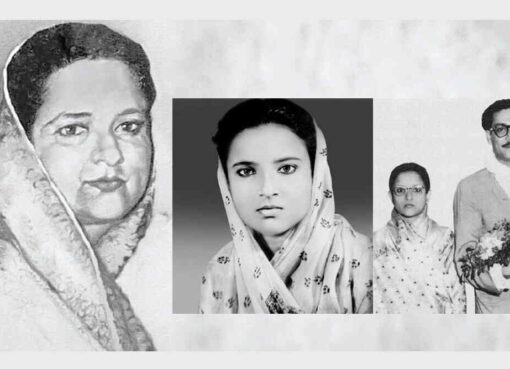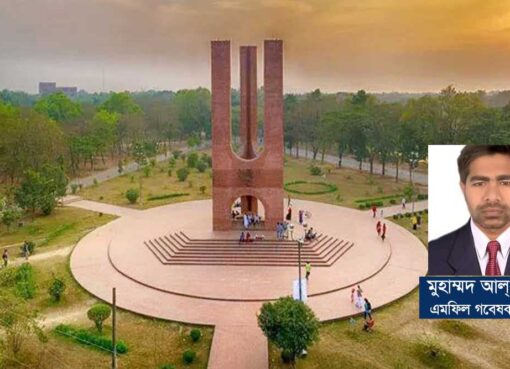নজরুল মুসলমান কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতাকে তিনি ‘ইসলাম গ্রহণ’ করতে দেননি। বাংলা ভাষায় অনবদ্য ইসলামি গজল রচনার কৃতিত্ব তাঁর। আজো বাঙালি মুসলমানের এক মাসের সিয়াম সাধনার পর রাতের আকাশে যখন চাঁদ ওঠে ইদের তখন বাংলার আনাচে কানাচে বেজে ওঠে ‘ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ইদ…’। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালি মুসলমান নজরুলকে সীমাবদ্ধ করে রাখল ‘মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই…’ এপিটাফে! তিনি মসজিদের প্রসঙ্গ এনেছেন ‘মানুষ’ বা ‘সাম্যবাদী’ কবিতাতেও। আমরা সেদিকে যাই না বললেই চলে। বাংলার না-পাঠকেরা নজরুলের ভক্ত সাজে মূলত রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে শাণিত করার জন্য। নজরুলকে পড়লে, তাঁকে আত্মস্থ করলে বাংলার দৃশ্যপট হতে পারতো অন্য রকম। নজরুল প্রকৃত ইসলামকে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ধর্মের আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন বাংলার মানুষকে। কিন্তু ধর্মের আলোয় বাংলার মানুষের চোখ ঝলসে যায়। তারা অন্ধকারে থাকতেই পছন্দ করে সম্ভবত। আর তাই নজরুল বাংলার মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, খণ্ডিত- ‘বিদ্রোহী’ ক্বচিৎ অবনত, ঈষৎ সংক্ষেপিত, পুরাণ পরিমার্জিত!
বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদান অনন্যসাধারণ। বাংলা কাব্য জগতে ‘বিদ্রোহী কবি’ নামে খ্যাত তিনি। নজরুল মানবতার কবি। বাংলা সাহিত্যের নতুন চণ্ডীদাস নজরুল, বাংলার যথার্থ চারণকবি। পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে প্রথমবার প্রত্যক্ষ করেছে- একই কবির দ্বৈত সত্তা। নজরুল একদিকে চরম বিদ্রোহী, অপরদিকে প্রচণ্ড বিরহী। রবীন্দ্র বটবৃক্ষতলে স্বতন্ত্র এক বটবৃক্ষ হয়ে ওঠেছিলেন নজরুল। বাংলা সাহিত্যে এ এক দুর্লভ ঘটনা। রবীন্দ্রযুগে যেসব কবি রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে কবিতা রচনা করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে। বাঙালির চিরায়ত ভাব-ভাষা নজরুলের কবিতায় পেয়েছে শিল্পিত ভাষ্য। তাই নজরুল আমাদের জাতীয় কবির মর্যাদার আসনে বসেছেন।
নজরুল একজন দুরন্ত স্বভাবের বালক হিসেবে গ্রামবাসীর কছে পরিচিত ছিলেন শৈশবে। হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানোই ছিল তাঁর স্বভাব। তাঁর জ্বালাতন থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি তাঁকে রাণীগঞ্জের কাছে শিয়ারশোল রাজস্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলের বাঁধাধরা জীবনের প্রতি অনাগ্রহ ছিল তাঁর। সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার কিছুদিন পরে ১৩/১৪ বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ ও বাড়ি থেকে পলায়ন করেন নজরুল। অতঃপর আসানসোল গিয়ে সেখানকার এক রুটির দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ করেন। কাজী রফিজউদ্দিন নামে আসানসোল থানার একজন দারোগা একদিন তাঁর কণ্ঠে গান শুনে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার কাজির সিমলা গ্রামে নিয়ে গিয়ে ত্রিশাল বাজারের নিকটবর্তী দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯১৪-র ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবার পরেই কাউকে কিছু না বলে কাজির সিমলা ত্যাগ করে রাণীগঞ্জে প্রত্যাবর্তন করেন। নিজের ইচ্ছায় পুনরায় শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ক্লাসে ভাল ছাত্র ছিলেন বলে তাঁর স্কুলের বেতন ও বোর্ডিং-এর আহার ছিল ফ্রি, তদুপরি রাজবাড়ি থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি লাভ করেন। বাউণ্ডুলে স্বভাবের এই কবি এক জায়গায় বেশি দিন থাকতেন না। তাইতো লিখেছেন ’বাঁধনহারা’ উপন্যাস। অনেকে এটিকে নজরুলের আত্মজীবনী বলে থাকেন। চিরব্যথী কবি তাই রচনা করেছেন- ‘ব্যথার সাগর পানিঘেরা চোরাবালির চর/ ওরে পাগল কে বেঁধেছিস সেই চরে তোর ঘর?’
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার। নজরুল কখনোই রবীন্দ্র-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হননি। অথচ বাংলার ঘরে ঘরে এমন কিছু মিথ্যা মিথ প্রচলিত আছে যেগুলো রীতিমতো ভয়ঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ কৌশল না করলে নোবেল পেতেন নজরুল (?) নজরুলকে এক আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাবিজ-কবজ করে তাঁকে পাগল বানিয়েছেন (?) নজরুল রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করতে পারতেন না… ইত্যাদি ইত্যাদি।
অথচ ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। হুগলি জেলে কারারুদ্ধ থাকার সময়ে কয়েদিদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট পালন করেন নজরুল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ মনীষী কর্তৃক নজরুলকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরণ করেন। প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায় প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম- ‘Give up hunger strike, our literature claims you’। ‘addressee not found’ মন্তব্য করে ডাক কর্তৃপক্ষ সে টেলিগ্রাম হুগলি জেলে নজরুলের কাছে না পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফেরত পাঠায়। ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট কলকাতা থেকে নজরুলের পরিচালনায় প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ধূমকেতুর আশীর্বাদ বাণীতে লেখেন- “কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু / আয় চলে আয় রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।”
নজরুলের ‘তীর্থ পথিক’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ করে লিখেছেন- “প্রার্থনা মোর, যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে / আসি যেন গাহন করিতে তোমার কাব্য গীতে।” পরাধীন জাতি সাম্রাজ্যবাদের শোষণে জর্জরিত হলে নজরুল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেন। ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ নাটকখানি নজরুলকে উৎসর্গ করে দেশবাসীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ উৎসর্গ ঘটনায় আপ্লুত কবি লেখেন- “আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে…।” নজরুলও তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ ‘সঞ্চিতা’ উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ শুনে নজরুল প্রচণ্ড আহত হলেন। লিখলেন অনবদ্য এক কবিতা ‘রবিহারা’ : “দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত পথের কোলে / শ্রাবণ মেঘ ছুটে এলো দলে দলে / উদাস গগন তলে / বিশ্বের রবি, ভারতের কবি / শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি / তুমি চলে যাবে বলে / বিদায়ের বেলায় চুম্বন লয়ে যায় তব শ্রীচরণে / যে লোকেই থাক হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে।” শুধু কবিতা নয় নজরুল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে গানও রচনা করেছিলেন- ‘ঘুমাইতে দাও, শান্ত রবিরে জাগায়োনা / সারাজীবন যে আলো দিল ডেকে তার ঘুম ভাঙায়োনা।’ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল জন্মগতভাবে ভারতের অহিংসার দর্শনে বেড়ে ওঠেছিলেন। অথচ আমরা না চিনলাম রবীন্দ্রনাথকে, না চিনলাম নজরুলকে।
একজন দাড়ি রাখল কিন্তু কলেমা পড়ল না এই আফসোসে মরি, আরেকজন চুল রেখে করল বিস্তর ভুল এই জ্বালায় জ্বলি।
নজরুল রাজনীতি সচেতন মানুষ ছিলেন। তাই রাজনীতিও করেছিলেন। ১৯২৫-এ ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেন নজরুল। এ সম্মেলনে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নজরুলের কণ্ঠে তাঁর ‘চরকার গান’ শুনে গান্ধীজী মুগ্ধ হন। অতঃপর কংগ্রেসের অঙ্গসংগঠন ‘মজুর স্বরাজ পার্টির’ (১৯২৫) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হন নজরুল। ১৯২৬ খ্রি. নভেম্বর মাসে ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় বিধান সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তমিজুদ্দীন খানের কাছে পরাজিত হন। কয়েক বছর আগে নেত্রকোণা থেকে কবি নির্মলেন্দু গুণও নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর নাকি জামানতের টাকাও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল! বাঙালি কেমন ইতর রাজনীতি করে বুঝেন। বাঙালি কবিদের মনে হয় বিশ্বাস করে না। কবিরা হয়তো ছন্দ বুঝে কিন্তু গমের হিসাব বুঝে কি? ১৯২৬-এর ২ এপ্রিল রাজরাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধলে এ বর্বরতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি কামনা করে ‘লাঙল’ পত্রিকায় অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ, গান ও কবিতা প্রকাশ করেন তিনি। অসাম্প্রদায়িক নজরুল একহাতে যেমন লিখেছেন ইসলামি গজল তেমনি আরেক হাতে লিখেছেন শ্যামাসঙ্গীত। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য সংগ্রাম করেছেন অক্লান্ত। তিনি লিখেছেন: ‘মোরা এক বৃন্তে ফুল হিন্দু মুসলমান / মুসলিম তার নয়নের মণি হিন্দু তার প্রাণ।’
ছোটবেলায় তাঁর নাম দুখু মিয়া হলেও তিনি ছিলেন আজন্ম দুখী। ১৯৩০-এ তাঁর চার বছরের প্রিয় শিশুপুত্র বুলবুল বসন্ত রোগে মারা গেলে শোকে মুহ্যমান হয়ে আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য বরদাকান্ত মজুমদারের কাছে অধ্যাত্ম-সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিশুপুত্রকে হারিয়ে তিনি লেখেন: ‘ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি…’
নজরুল ইসলামি গানের পাশাপাশি অন্যান্য গানও রচনা করেছেন প্রচুর। গানের সংখ্যায় তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ১৯২৯-এর ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে তাঁকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা সভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর সভাপতির ভাষণে নজরুলকে ‘প্রতিভাবান বাঙালি কবি’ বলে আখ্যায়িত করেন। একই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু কবিকে সম্ভাষন করে বলেন, ‘আমরা যখন যুদ্ধে যাব, তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব’।
বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি তাঁর থেমে যাওয়ার কারণটাও ভয়ঙ্কর। ১৯৪২-এর ১০ অক্টোবর মস্তিস্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন নজরুল। কিছুকাল পরে চৈতন্য ও বাকশক্তি লোপ পাওয়ায় তাঁর সাহিত্য-সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থায় জীবনযাপন করেন বাংলার এই প্রতিভাবান কবি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২-এর ২৪ মে তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনা হয়। নজরুল ও প্রমীলা দম্পতির চারজন ছেলে সন্তান- ১. কৃষ্ণ মোহাম্মদ ২. অরিন্দম খালেদ বুলবুল ৩. কাজী সব্যসাচী ৪. কাজী অনিরুদ্ধ। এঁদের মধ্যে প্রথম দুইজন অকালে মারা যান। কাজী সব্যসাচী (১৯২৯-১৯৭৯) ও কাজী অনিরুদ্ধ (১৯৩১-১৯৭৪) বেঁচে ছিলেন। কবিপুত্র সব্যসাচী ছিলেন আবৃত্তিশিল্পী, এবং অনিরুদ্ধ ছিলেন সুরকার। সব্যসাচীর কন্যা খিলখিল কাজী ও অনিরুদ্ধর কন্যা অনিন্দিতা কাজীর মাধ্যমে কবির উত্তর-প্রজন্ম এখনো টিকে আছে। নজরুলের স্ত্রীর নাম আশালতা সেনগুপ্ত। তাঁর ডাকনাম ছিল দুলি। নজরুল তাঁর স্ত্রীর নাম পাল্টে রাখেন প্রমীলা। প্রমীলার জন্ম ১৯০৮ সালের মে মাসে। তাঁদের বিয়ে হয় ১৯২৪ সালে। ১৯৩৯ সালে প্রমীলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি আর সুস্থ হননি। টানা তেইশ বছর তিনি শয্যাগত ছিলেন। ১৯৬২ সালের ২৩ জুন তিনি মারা যান। নজরুল এর পরও বেঁচে ছিলেন অনেকদিন।
নার্গিস-নজরুলের প্রেম নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। নজরুলের চরিত্রকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেন অনেকে। ঘটনা মূলত এমন: নজরুলের বিয়ের আগে, ১৯২১ সালে নজরুল দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে আসেন। কুমিল্লার পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী আলী আকবর খানের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। তাঁর অনুরোধে নজরুল ‘লিচুচোর’ কবিতাটি লিখেছেন। আলী আকবর খানের সঙ্গেই নজরুল কুমিল্লায় আসেন ১৯২১ সালে। আলী আকবর খানের এক ভাগনির নাম সৈয়দা খাতুন (মুন্সী আবদুল খালেকের কন্যা )। সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের প্রণয়ভাব হয়েছিল। নজরুল ইরানি ফুলের নামে তার নামকরণ করেন নার্গিস। কবির প্রিয়া নার্গিসের নামে যে গান কবিতা পাওয়া যায় সেই নার্গিসই মূলত সৈয়দা খাতুন। কবির সাথে বিয়েও ঠিক হয়েছিল। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৩ আষাঢ় ছিল বিয়ের দিন। বিয়ের আমন্ত্রণ পত্রও মুদ্রিত হয়েছিল। অনেকে বলেন নজরুল বিয়ের আসর থেকে ওঠে পায়ে হেঁটে দৌলতপুর থেকে চলে যান কুমিল্লা। আবার অনেকে বলেন তাঁদের আকদ হয়েছিল। তবে তথ্যদুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেকে যায় কিন্তু তাঁদের প্রণয় নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর সম্পূর্ণ তথ্য জানার জন্য আরো গবেষণা প্রয়োজন। ১৯৩৭ সালে সৈয়দা খাতুনের বিয়ে হয় কবি আজীজুল হাকিমের সঙ্গে। সৈয়দা খাতুন ‘তহমিনা’ নামে একটি উপন্যাস লেখেন।
বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের দীপ্র আবির্ভাব মানবতার জয়গান নিয়ে। ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণতূর্য’- এই ছিল নজরুল সাহিত্যের মূল কনসেপ্ট। নজরুলের বিরহী ও বিদ্রোহী সত্তা বাংলা সাহিত্যে যোগ করেছিল নতুন মাত্রা। নজরুলের বিদ্রোহ ছিল মানবতার পক্ষে, সমাজপতিদের বুকে তিনি এঁকে দিতে চেয়েছেন পদচিহ্ন। তিনি কুলি-মজুর, কৃষক, শ্রমিক, বারবনিতাসহ সকলকে তাঁর সাহিত্যে অন্তুর্ভুক্ত করেছেন। কাউকে বাদ দেননি নজরুল।
মানুষের দুঃখে নজরুলের হৃদয় সাহারার মতো আর্তনাদ করে উঠত। ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’(১৯৩০) উপন্যাসে আছে ক্ষুধার জ্বালায় ধর্মান্তরিত হওয়ার কাহিনি। কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়ক এলাকার দিনমজুরেরা এই উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। সংগ্রামে পর্যুদস্ত এসব নিরক্ষর মানুষের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি আছে এ উপন্যাসে। নিম্নবর্গের নারীর সংগ্রামী জীবন অঙ্কিত হয়েছে ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’ উপন্যাসের মেজোবৌ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নজরুলের ছোটগল্পেও নিম্নবর্গের মানুষ এসেছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাব ও ভাষায়। ‘রাক্ষসী’ গল্পে প্রান্তিক নারীর জীবন-সংগ্রাম, প্রেম, প্রতিশোধ চিত্রিত হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষও প্রয়োজনে হতে পারে বিদ্রোহী, অধিকার আদায়ে করতে পারে জীবনকে বিপর্যস্ত, নিম্নবর্গের মানুষও কথা বলে ওঠে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে- এমন সত্যকে নজরুল দেখিয়েছেন ‘রাক্ষসী’ গল্পে। নজরুলের নিম্নবিত্তরা বাস করে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য এলাকায়, এরা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, ব্যথাহত বাঙালি সমাজের প্রান্তবাসী মানুষ। নজরুল এসব ব্রাত্যবাসী মানুষের হৃদয়ের ক্ষত, তাদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবালেখ্য রচনা করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।
বাঙালির বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম- তিনি বাংলা সাহিত্যের আঁধারে বেঁধেছিলেন অগ্নিসেতু, তিনি বাংলা ভাষার ধূমকেতু। বিদ্রোহী নজরুল সকলকে ছেড়ে ওঠেছিলেন সর্বোচ্চ শিখড়ে- ‘আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।’ নজরুলের বিদ্রোহ ছিল মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই নজরুল উচ্চাসনে বসে হুঙ্কার দেন- ‘আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না / অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।’ ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় নজরুল বিদ্রোহীর ভয়ঙ্কর সব অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কখনো শিব, কখনো ইসরাফিলের শিঙা, কখনো জিবরাইলের ডানা আবার কখনো অর্ফিয়াসের বাঁশি- এমনই পুরাণ ও ইসলামি নানা প্রতীকে বিপ্লবী নজরুল তাঁর স্বরূপ চিনিয়েছেন। নজরুলের বিপ্লব ছিল সমাজপতিদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা লিখে তিনি জেলে গিয়েছিলেন। তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল বলে। নজরুলের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা ছিল বজ্রনিনাদের মতো। তাঁর ‘বিঁষের বাঁশি’, ‘ভাঙার গান’, ‘প্রলয়শিখা’, ‘যুগবাণী’, ও ‘চন্দ্রবিন্দু’ রচনা সমূহে বিদ্রোহের প্রবলসুর ধ্বনিত হয়েছে। মহাকাব্য রচনা না করার অভিযোগের জবাবে নজরুল জানিয়েছিলেন- ‘বড় ভাব বড় কথা বন্ধু আসে না’ক মুখে / অমর কাব্য তোমরা লিখিও আছো যাহারা সুখে।’ নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা উচ্চকিত ছিল প্রান্তবাসী মানুষের অধিকার আদায়ের অভিপ্রায়ে।
নজরুল চর্চা এদেশে হয় না বললেই চলে। নজরুল সাড়ে তিন হাজারের মতো গান লিখেছেন কিন্তু আমরা তাঁর কয়টা গান শুনেছি। আমরা পড়ার চেয়ে নজরুল-রবীন্দ্র কে বড় কবি এসব তর্কেই সময় ব্যয় করি সবচেয়ে বেশি। দুজনের মূল দর্শন যে একই সুতোয় বাঁধা তা আমরা জানতেও চাই না। ছোটবেলা হতেই আমাদের মনে ধর্মান্ধতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ছোটবেলায় শোনা একটি ছড়া খুব মনে পড়ছে : “কাজী নজরুল তুমি করেছিলে ভুল / দাড়ি না রেখে রেখেছিলে চুল ।” কে, কখন এই লাইন দুটো লিখেছিল জানি না তবে এ লেখার উদ্দেশ্য কী তা বুঝার জন্য বুদ্ধিজীবী হতে হয় না।
একটি শোনা কথা: মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনো এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ চালিয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারি। সেখানের একটি কক্ষে তারা দেখল পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দুটি ছবি টানানো। পাকিস্তানি এক অফিসার কোনো এক সেপাইকে হুকুম দিল ছবিগুলো টেনে নামানোর। তাদের মধ্যে থাকা একজন অনুরোধ করল লম্বা আলখাল্লাপরা দাড়িওয়ালা হুজুরের ছবিটা রেখে দিতে! আর বাঁশি হাতে লম্বা চুলওয়ালা হিন্দু লোকের ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে!
বাঙালির রবীন্দ্র-নজরুল চর্চা পাকিস্তানি মিলিটারিদের উপর্যুক্ত গল্পের বাইরে যেতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।